সুজিৎ চট্টোপাধ্যায় : কলকাতা, ১০ এপ্রিল ২০২২। এই বছর এই দিনে রামনবমী পালিত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অস্ত্রমিছিল করে জাঁকজমকভাবে পুরুষোত্তম রামের জন্মদিন পালন করছেন। দুবছর করোনা পরিস্থিতিতে জমকালো ভাবে রামনবমী পালন না করার দুঃখ, এবার রাম ভক্তরা সুদে আসলে পুষিয়ে নেবেন। তবে নিন্দুকরা বলেন, রামের প্রতি শ্রদ্ধার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির এক কৌশল ছাড়া বিষয়টি আর কিছু নয়। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৮ র ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যের কয়েকটি প্রাচীন ধারায় সংগঠিত মিছিল ছাড়া অস্ত্র নিয়ে মিছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু সেবছর উৎসব শান্তিপূর্ণ হয়নি। সাম্প্রদায়িক উস্কানির বলি হন এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র।
 চরম সংযমের পরিচয় দিয়ে নিহত পুত্রের পিতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, রক্তের বদলা রক্ত নয়। কারোর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগও জানান নি। তবে বেশ কিছু মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে রাজ্যের এক ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াহিয়া সেই ঘটনার জন্য তৎকালীন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে দায়ী করেছিলেন। এবার সেই বাবুল যখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে বালিগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী হলেন, সেই সব সংগঠন আন্দোলনে দাবি তুললেন, ছাত্রের খুনে হাত রাঙিয়েছেন যে বাবুল, তাঁকে যেন মানুষ ভোট না দেয়। এবারেও রামনবমী উদযাপন যে শুধু বিজেপি বা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন করছে তা নয়। রাজ্যের শাসকদলের উৎসাহীরাও রামনবমী পালন করে প্রমাণ করতে চলেছেন হাম কিসিসে কম নেহি। সূত্রের খবর, রাজ্য জুড়ে বিজেপি যেমন একহাজার শোভাযাত্রা করবে, তেমন দলীয় পতাকা ছাড়া তৃণমূল দলের সমর্থকরাও শোভাযাত্রার আয়োজন করছে। পর্যবেক্ষকদের অনুমান, সামনের বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই হিন্দু ভোট একজোট করতে দুদলের এই প্রয়াস। ২০১৮ তে আমরা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি ত্রিশূল হাতে দুর্গা সেজেছিলেন । সেই বছর তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তীকে দেখা গেছে এক বিজেপি নেতার সঙ্গে পা মিলিয়ে রামনবমীর মিছিলে হাঁটতে।
চরম সংযমের পরিচয় দিয়ে নিহত পুত্রের পিতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, রক্তের বদলা রক্ত নয়। কারোর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগও জানান নি। তবে বেশ কিছু মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে রাজ্যের এক ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াহিয়া সেই ঘটনার জন্য তৎকালীন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে দায়ী করেছিলেন। এবার সেই বাবুল যখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে বালিগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী হলেন, সেই সব সংগঠন আন্দোলনে দাবি তুললেন, ছাত্রের খুনে হাত রাঙিয়েছেন যে বাবুল, তাঁকে যেন মানুষ ভোট না দেয়। এবারেও রামনবমী উদযাপন যে শুধু বিজেপি বা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন করছে তা নয়। রাজ্যের শাসকদলের উৎসাহীরাও রামনবমী পালন করে প্রমাণ করতে চলেছেন হাম কিসিসে কম নেহি। সূত্রের খবর, রাজ্য জুড়ে বিজেপি যেমন একহাজার শোভাযাত্রা করবে, তেমন দলীয় পতাকা ছাড়া তৃণমূল দলের সমর্থকরাও শোভাযাত্রার আয়োজন করছে। পর্যবেক্ষকদের অনুমান, সামনের বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই হিন্দু ভোট একজোট করতে দুদলের এই প্রয়াস। ২০১৮ তে আমরা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি ত্রিশূল হাতে দুর্গা সেজেছিলেন । সেই বছর তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তীকে দেখা গেছে এক বিজেপি নেতার সঙ্গে পা মিলিয়ে রামনবমীর মিছিলে হাঁটতে।
আসলে ভোট বড় বালাই। সে প্রসঙ্গ না হোক উহ্য থাক। ফিরে যাই রামনবমী প্রসঙ্গে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের একাংশের বক্তব্য, হিন্দি গো বলয়ের আর্য সংস্কৃতির আগ্রাসন ঘটাতেই বাংলার অনার্য সংস্কৃতিকে গিলে খাওয়ার এক কৌশলী প্রচেষ্টা। বাংলায় রামনবমীর প্রাক্কালে বাংলার মানুষ কিন্তু মেতে ছিলেন অন্নপূর্ণা পুজোয় এবং বাসন্তী পুজোয়। কিন্তু রামনবমী পালনের ঘটনাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। আসুন বরং দেখা যাক, রামচন্দ্র প্রসঙ্গ। মূলত পুরানকে অবলম্বন করেই রাম ভক্তরা রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানেন। অবতার কাকে বলে? সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধান বলছে, দেবতারা সময়ে সময়ে মনুষ্য মূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আগমন করেন। স্বয়ং ভগবান (পূর্ণ ব্রহ্ম) বা তাঁর অংশে জীবদেহ পূর্ণাবতার বা অংশাবতার রূপে ধরাধামে অবতরণ করেন এবং অধর্মের নাশ (?) ধর্ম সংস্থাপন এবং জীবোদ্ধার করেন। রামায়ণের সমাজ গ্রন্থে কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, রামের অবতারভুক্তি বুদ্ধদেবকে অবতারভুক্তি করার পর । সে এক রহস্য। এই প্রতিবেদনে যা বলতে গেলে প্রতিবেদন দীর্ঘ হয়ে যাবে। পাঠকের অনুরোধ পেলে বারান্তরে জানাবার ইচ্ছে রইলো।
কিছু গবেষকদের ধারণা, রামায়ণের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতক। কেউ বলেন, চতুর্থ শতক। লক্ষ্য করবেন, কৃষ্ণের জন্মদিনে কেন্দ্রীয় ছুটি।রামনবমীতে নয়। ২০১৫ তে ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চের তরফে এক প্রদর্শনী হয় দিল্লিতে। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের তৎকালীন সংস্কৃতি মন্তেই মহেশ শর্মা। প্রদর্শনীর নাম ছিল ঋকবেদ থেকে রোবোটিক্স। ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর সরোজ বালা জানান, ৭হাজার টাকা দিয়ে তাঁরা একটি সফটওয়্যার আনান আমেরিকা থেকে। সেই সফটওয়্যার থেকেই নাকি জানা গেছে, রামের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫১১৪ বছরে ১০ জানুয়ারি বেলা ১২ টা ৫মিনিটে। এর আগে ড: পি ভি বর্তক জানিয়েছিলেন, রামের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২৩ এর ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। বনবাস ৭৩০৬ খ্রিস্টপূর্ব ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ,দশরথের মৃত্যু খ্রিস্টাব্দপূর্ব ৭৩০৬ এর ৫ ডিসেম্বর,রাবণের মৃত্যু ৭২৯২, ১৫নভেম্বর, রবিবার। তাহলে এপ্রিল মাসে রাম নবমী? হিসেব কি মিলছে?
যাক আসল কথায় আসা যাক। বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছেন। তাঁর রামায়ণে অকালবোধন নেই। এমনকি হিন্দিতে লিখিত তুলসীদাসী রামায়ণেও অকালবোধন নেই। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ টুকতে গিয়ে অকালবোধনের গপ্পো জুড়েছেন। আমরা সেই হিসেব মেনে দুর্গাপুজো করছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ না থাকা সত্বেও বাংলা রামায়ণে অকাল বোধনের গল্প কেন জুড়লেন? বিস্তারিত তথ্যে না গিয়ে এটুকু বলাই যায়, সংস্কৃত থেকে প্রথম বাংলায় রামায়ণ অনুবাদক কিন্তু কৃত্তিবাসকে বলা যায় না। বরং বাংলা রামায়ণের নতুন রচনাকার বলা যায়। কৃত্তিবাস ছিলেন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত প্রেমতলি গ্রামের কাছে। মতান্তরে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ফুলিয়াগ্রামের। পিতা বনমালী ওঝা। পিতামহ মুরারী ওঝা। ইতিহাস বলছে, পূর্ববঙ্গ থেকে বেদানুজ রাজার সভাপন্ডিতনরসিংহ মুকুটি (মুখোপাধ্যায়) চলে আসেন নদীয়ায়। তাঁর পুত্র গর্ভেশ্বর। তাঁর পুত্র মুরারী। মুরারীর সাতপুত্রের একজন বনমালী। বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস। ছয় ভাইয়ের মধ্যে কৃত্তিবাস ছিলেন বড়। কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ রচনার ভার নেন, সহযোগী ছিলেন কিছু পন্ডিত। তাঁদের কেউ ছিলেন শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব। ফলে দুই হিন্দু ধর্মের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব কাব্যে ফুটে ওঠে। কোথাও বৈষ্ণব কোথাও শাক্ত ধর্মের প্রভাব।অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্রের সংঘাত। অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতি ও অনার্য সংস্কৃতির ঠান্ডা লড়াই। কৃত্তিবাসের কথায় ফিরে আসি।
গৃহশিক্ষার পর বারো বছর বয়সে কবি যান উত্তরবঙ্গে। বাসনা ছিল রাজপন্ডিত হওয়া। সূত্র বলে, গৌড়েশ্বর গণেশ (১৪১৫-১৪১৮) মতান্তরে সুলতান জালালউদ্দিন (১৪১৮-১৪৩১) এর দরবারে বাংলা শ্লোক শুনিয়ে উপঢৌকন পান। গৌড়েশ্বর তাঁকে পয়ার ছন্দে বাংলা রামায়ণ রচনার অনুরোধ করেন। মনে রাখা দরকার, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছিল পুঁথিতে। সেই পুঁথি কোথায়? কে উত্তর দেবে? সেই পুঁথির প্রামাণ্য নথি কই? প্রথম বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঁচ খন্ড ছাপা হয়, ১৮০২ সালে। উইলিয়াম কেরির শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। তখনও বাংলার ব্রাহ্মণকূল আপত্তি জানাতেন সংস্কৃত ভাষার রামায়ণ বাংলায় লেখা পাপ। কিন্তু জনপ্রিয়তায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ১৮৩৩-৩৪ সালে দুখন্ডে সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৭৬২ সালে রামানন্দ ঘোষ একটি রামায়ণ রচনা করেন। যেখানে রামচন্দ্রকে বুদ্ধের অবতার বলেছেন । কৃত্তিবাসি রামায়ণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন , কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতাব্দী) সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।,,,,কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিপুল প্রচারলাভ করিবার ফলে লোকমুখ এত পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস রচিত মূলত রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমান প্রচলিত কৃত্তিবাসি রামায়ণ এর মধ্যে অবশিষ্ট নাই। তিনি (কৃত্তিবাস) বাল্মীকির রামায়ণ কে অবিকলভাবে অনুসরণ করেন নাই।(৩৭০ পৃষ্ঠা)।
কলকাতার র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন প্রকাশনা থেকে কঙ্কর সিংহ’ তাঁর ধর্ম ও নারী প্রাচীন ভারত’ গ্রন্থে রামায়ণ ও নারী প্রবন্ধে লিখেছেন, রামায়ণের মূল কাহিনী শুরু হয়েছে অপুত্রক রাজা দশরথের পুত্রলাভের কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মাধ্যমে। যে যজ্ঞ করে রাজা দশরথ তিন রাণীর কাছ থেকে চার পুত্র পান ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির স্পন্সরশিপে। এই তিন প্রধান রাণী ছাড়া আরও তিনশত পঞ্চাশজন পত্নী ছিল রাজা দশরথের। যাদের কাছ থেকে দশরথ কোনও পুত্র লাভ করতে পারেননি। রাম বনবাসে যাওয়ার আগে এঁদের প্রণাম করে যান। কৃত্তিবাস রামায়ণে দশরথের ৭৫০ জন রাণীর কথা বলেছেন। লিখেছেন, পুত্রহীন মহারাজা মনে দুঃখ দাহ, করিলেন সাতশত পঞ্চাশ বিবাহ। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস গবেষক কল্যাণী বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, আসলে একথা মনে করার অনেক কারণ আছে যে রামায়ণের চার নায়ক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নর প্রকৃত পিতা ছিলেন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ। পূত্রেষ্টি যজ্ঞের অনেক আগেই দশরথ পুত্রকলত্র বিশিষ্ট ঋষিকে অযোধ্যায় এনে অন্দরে প্রবেশ করাইয়া অতিথি সৎকার করেন। ঋষি একবৎসরকাল বাস করার পর দশরথ তাঁকে বলেন, সুব্রত, যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয় আপনি এইরূপ কার্য অনুষ্ঠান করুন। পাঠকদের এবার ঋষির পরিচয় দিই। ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতি পুত্র কাশ্যপ। কাশ্যপ পুত্র বিতান্ডক মুনি। বিতান্ডক একদিন তপস্যার ক্লান্তি দূর করতে একটি হ্রদে স্নান করতে গিয়ে স্নানরতা অপ্সরা উর্বশীকে দেখে জলমধ্যে বীর্যপাত করেন। এক তৃষিত হরিণী সেই বীর্যমিশ্রিত জলপান করে গর্ভিনী হয়। জন্ম হয় ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ’র। পরবর্তীকালে আবার ঋষি বিয়ে করেন রামের দিদি শান্তাকে। অর্থাৎ পিতা হলেন জামাইবাবু। সংস্কৃত সাহিত্যের বৃটিশ অধ্যাপক ড: জে এন ব্রুকিংটন তাঁর ‘ন্যায়পরায়ন রাম’ গ্রন্থে লিখেছেন, দশরথ রামকে উত্তরসূরি ঘোষণা করতেই কৈকেয়িকে মন্থরা দাসী বলে- রামের রাজা হওয়ার খবরে রামের রাণীরা খুশি হবে, তোমার পুত্রবধূ কষ্ট পাবে। রামের অভিষেকের সময় শত্রুঘ্ন সাজিয়েছেন রামকে, রামের পত্নীদের সাজিয়েছেন কৌশল্যা। রাম জন্মের পর দিদি শান্তাকে দেখেননি। তাঁর আগেই গলগ্রহ কন্যাকে দশরথ বড়রাণী কৌশল্যার বোন ভার্যিনী ও তাঁর স্বামী রাজা লোমপাদকে দত্তক দেন। এই তথ্যের সমর্থন মেলে বিবেকানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত এর প্রবন্ধে। যেখানে লেখক তুলে ধরেছেন রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৮ম সর্গ। সেখানে দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে বলছে, হৃষ্ঠা খলু ভবিষ্যন্তি রা পরমা: স্ত্রিয়:/ অপহৃষ্ঠা ভবিষ্যন্তি স্নুষান্তে ভরত ক্ষয়ে ২/৮/১২,সাং সং ২/৮/৫। যার বাংলা অর্থ, রাম রাজা হলে তোমরা দুঃখ পাবে আর রামের স্ত্রীরা সুখে থাকবে। ভরতের স্ত্রী দুঃখ পাবে। রামের বহু স্ত্রীর উল্লেখ আছে সি আর শ্রী নিবাস ইয়াঙ্গারের অযোধ্যা কাণ্ডম এ্যইটথ চ্যাপ্টার গ্রন্থের ২৮পৃষ্ঠায়। যেখানে বলা হয়েছে বাল্মীকি রেফার্স টু দ্য মেনি ওয়াইভস। রামচন্দ্র মোটেই পুরুষোত্তম নন। বরং রাবণ উৎকৃষ্ট। একথা বলেছেন বিবেকানন্দ তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ১১৩নম্বর পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন, রাবণ রামায়ণ পড়ে দেখ, রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে কমতো নয়ই, বরং বেশি ছিল।
পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সীতা উদ্ধারের জন্য বানর সুগ্রিবের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল রামের। সুগ্রীবের সঙ্গে প্রণয় ছিল তাঁর বৌদি তারার। সেকথা জেনে ভাইকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন কিস্কিন্ধ্যার রাজা বালী। সুতরাং বালী বধ না হলে সুগ্রীবের রাজা হওয়া সম্ভব নয়। তাই দুই ভাইকে লড়িয়ে দেন রাম। সুগ্রীব পরাজিত হচ্ছেন দেখে ছলের আশ্রয় নিয়ে রাম বালীকে বধ করেন। মৃত্যুশয্যায় বালী রামচন্দ্রকে বলেন, পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মণ ক্ষয়েষু রাঘব শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গঃ কূর্মশ্চ। পঞ্চমা ৷ ১৬/৩৫ অভক্ষ্যাণি চ পঞ্চৈব যানি রামশ্রুতানি মেশগালশ্চৈব নক্রশ্চ বানরঃ বিন্নরো নরঃ | ১৬/৩৬, অর্থাৎ, হে রাঘব, পাঁচ নখর বিশিষ্ট প্রাণীকে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা হত্যা করে খায় আমি জানি। তারা হলো খরগোশ, সজারু, গোসাপ, গণ্ডার আর কচ্ছপ। কিন্তু শিয়াল, কুমির, বানর, কিন্নর ও নর খাওয়া নিষিদ্ধ। আমি তো বানর। তাহলে আমাকে হত্যা করলে কেন? রামনবমীর প্রাক্কালে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের ভক্তরা নিজেরা নিরামিষাশী হওয়ার সুবাদে আপত্তি করেন, যেন কেউ মাছ মাংস না খান। ইতিমধ্যে দিল্লিতে নব রাত্রির দিনগুলিতে মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মেয়র। অথচ রামচন্দ্র যে মাংস রসিক ছিলেন সেকথার উল্লেখ মেলে বাল্মীকি রামায়ণে। সেখানে অযোধ্যা কাণ্ডে মাতা কৌশল্যার কাছে রাম শপথ করছেন, চোদ্দো বছর বনবাস কালে তিনি কন্দমুল ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করবেন। আবার অযোধ্যা কাণ্ডের ৫২/১০২ সুক্তে লেখা রাম বনবাসে পশু শিকার করে মাংস খাচ্ছেন। দীপা বন্দোপাধ্যায়ের মহাকাব্যের রসুই ঘরে গ্রন্থে লেখিকা লিখেছেন,,গঙ্গা পার হয়ে সুমর আর গুহককে বিদায় দিয়েই গভীর অরণ্যে রাম আর লক্ষ্মণকে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল।সঙ্গে ছিলেন জনকনন্দিনী সীতা। তখন ভীষণ ক্ষুধা তাঁদের গ্রাস করেছিল। অতএব নান্য: পন্থা: পথ নেই।অরণ্যে প্রবেশ মাত্রই তাঁরা দুই ভাই হত্যা করলেন চারটি বিশাল আকৃতির পশু বরাহ (bour),. ঋষ্য ( The printed or white footed antisope). পৃষত The spotted anteiope). মহারুর (a species of antelope)। বনবাসকালে কালিন্দী নদী পেরোনোর সময় স্বামীর দুর্ভাগ্য মোচনে সীতা নদী মাতার কাছে মানত করে বলেন, প্রতিজ্ঞা পালন করে অযোধ্যায় ফিরে এসে মাংসের পোলাও ও সহস্র কলস সূরা দিয়ে পুজো দেবেন।
রামের তো জন্মই হতো না, যদি না নারদ বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতেন। কি সেই অভিশাপ? পুরাণ বলছে, দেবর্ষি নারদের মনে দুঃখ ছিল, তিনি দেখতে সুপুরুষ নন। একবার এক সুন্দরী রাজকন্যার প্রেমে পড়েন নারদ। তিনি বিষ্ণুর কাছে তাঁকে সুন্দর মুখশ্রী দান করতে বলেন। তিনি যেন রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় সফল হন। বিষ্ণু তাঁকে রূপদান করেন। মনের আনন্দে স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যার পানিপ্রার্থি হন নারদ। রাজকন্যা বরমাল্য নিয়ে যখন পানিপ্রার্থীদের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই দলে অপেক্ষমান নারদের সামনে এসে হেসে লুটিয়ে পড়েন রাজকন্যা। কারণ মস্করা করে বিষ্ণু নারদের মুখে এক বানরের মুখ বসিয়ে দেন। বিষ্ণুর এই মস্করাতে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ নারদ বৈকুণ্ঠে এসে বিষ্ণুকে শাপ দিয়ে বলেন, তিনি যেমন স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হলেন, তেমনই বিষ্ণুকে স্ত্রী বিরহে ভুগতে হবে। তাই বিষ্ণুকে রামরূপে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। রাম তো হনুমান আর লক্ষণকে হত্যা করার সংকল্পও নিয়েছিলেন। পুরাণ বলছে, রামের পরম ভক্ত হনুমান। হনুমান কে?
যুক্তির নিরিখে বলা যায়, রাম সূর্যবংশীয় আর্য পুত্র। হনুমান আদতে অনার্য । ভারতের ভূমিপুত্র। সুতরাং হনুমানকে রামের ভক্ত না বানালে আর্য সংস্কৃতির পদতলে অনার্য সংস্কৃতির বশ্যতার প্রতীক স্থাপন হয় কী করে? বিষয়টি যে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধও আছে। বিশ্বভারতী সাহিত্য ১৪০১ সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধে ১০৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ‘,,,,_ রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে ( এই) দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন, এই কারণেই তাহার গৌরব গান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।’ একবার নারদ লক্ষ্য করেন, বিষ্ণুর অবতার রাম তাঁর চেয়ে হনুমানকে বেশি স্নেহ করছেন। তাই লঙ্কাজয় করে রাম ফিরে এলে কূলগুরু বিশ্বামিত্রসহ বহু ঋষি যখন আসেন রামকে অভিনন্দন জানাতে, রামচন্দ্র তাঁদের সেবার ভার দেন হনুমানকে। নারদ হনুমানের কাছে গিয়ে জানান, বিশ্বামিত্র ঋষি হনুমানের বিরুদ্ধে রামের কান ভারি করছেন। সুতরাং অন্য ঋষিদের আপ্যায়ন করলেও হনুমান যেন বিশ্বামিত্রকে অবজ্ঞা করেন। সরল আদিবাসী হনুমান নারদের কথা বিশ্বাস করে বিশ্বামিত্রকে অবজ্ঞা করেন। অপমানিত বিশ্বামিত্র রামকে আদেশ দেন, হনুমানকে প্রাণদণ্ড দিতে। গুরুর আদেশ মেনে রামচন্দ্র হনুমানকে বধ করার সিদ্ধান্ত নেন। নারদ বেগতিক দেখে বিশ্বামিত্রকে আসল কথা জানিয়ে হনুমানের প্রাণরক্ষা করেন। লক্ষ্মণকেও রামচন্দ্র বধের সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন। সেও এক ব্রাহ্মণের আদেশে।
রামের সঙ্গে সীতার সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা আছে। দুজনের প্রেম ছিল যেকোনও দম্পতির জন্য আদর্শ। কিন্তু রাবণের বন্দিনী সীতা যখন ফিরে এলেন, রামের কি বক্তব্য ছিল? বিষয়টি জানতে শরণাপন্ন হচ্ছি রাজশেখর বসুর । তিনি লিখছেন, ‘পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। কিন্তু উত্তর কবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। একি নিষ্ঠুরতা না উৎকট আদর্শ প্রীতি?…. রাম কোনোদিনই সীতার চরিত্র বুঝতে পারেননি,সে মানসিকতাও তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। অগ্নিপরীক্ষার সময় থেকেই সীতা উপলব্ধি করলেন, দীর্ঘ ২৫বছরের একান্ত সাহচর্য সত্ত্বেও তিনি রামকে বুঝতে একেবারেই ভুল করেছেন। বাহুবল রামচন্দ্রের থাকলেও বীরত্ব তাঁর ছিল সীতার কাছে রাম কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে লাগলেন।রামের অপমান, কটুক্তি গালিগালাজ শুনে সীতা চোখের জল মুছেছিলেন।(যুদ্ধ কাণ্ড সর্গ ১১৬-১১৮৮)। সুকুমারী ভট্টাচার্য বাল্মীকি রামায়ণের উল্লেখ করে বলেছেন, রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করার সময় বলেছিলেন,সে যেন সুগ্রিব বা বিভীষণকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন। সীতা সেকথা প্রত্যাখ্যান করেন।y,,,,, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রামচন্দ্র জানলেন বনবাসে গিয়ে সীতা মারা যাননি। তিনি ভাবতেও পারেননি সীতা এতদিন জীবিত আছেন। খোঁজ নেওয়ারও দরকার মনে করেননি রাম। ধরে নেন সীতা মৃত। তাই স্বর্ণসীতা বানিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এরপর যখন তিনি সন্ধান পেলেন,সীতা জীবিত, তিনি সিদ্বান্ত নেন, সীতাকে বাঁচতে দেওয়া যায় না। ,,,,,’সীতার পাতাল প্রবেশ এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে প্রশান্ত প্রামাণিক ঋকবেদ সংহিতা(হরফপ্রকাশনী), অথর্ব বেদ সংহিতা, বাল্মীকি রামায়ণ রাজশেখর বসু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস , ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ,রামায়ণ খোলা চোখে গ্রন্থের লেখক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঋকবেদ , নক্ষত্র বেলাবাসিনী ও অহনা গুহ ও অনান্য সূত্র থেকে তথ্য নিয়েছেন।
তাড়কা রাক্ষসীর নামে আসলে এক আদিবাসী মহিলাকে কিশোর বয়সে প্রথম নারী হত্যা করে জীবন শুরু করেন রামচন্দ্র। কি ছিল সেই আদিবাসী নারীর দোষ? তাঁদের বনভূমিতে বহিরাগত ঋষিরা এসে বনাঞ্চলের গাছ কেটে যজ্ঞে জ্বালানি হিসেবে এবং ঘি দিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে পরিবেশ দূষণ এবং জোরে জোরে সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রচ্চারণ করে শব্দদূষণ করতেন। বনের পশুপাখি ভীত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত। তার বিরোধিতা করেছিলেন আদিবাসী রমণী তাড়কা । রামের শুদ্রহত্যার কাহিনী শম্বুক বিষয়টি আর নতুন করে বলার নেই। সবচেয়ে বিস্ফোরক তথ্য পেয়েছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায়। সংবাদসূত্র ইউএনআই। সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল তা হুবহু তুলে ধরছি।, রাজা দশরথ কে হত্যা করেছিলেন রামচন্দ্র। লেখা আছে অ্যাসিরিয়ান প্রাচীন পুঁথিতে। মিশরে রাম সূর্যদেবতা হিসেবে পূজিত হন। রামায়ণেও তাঁকে সূর্যবংশীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ড: সুকুমার সেনের ‘রামায়ণ কথা’ গ্রন্থে সীতার জন্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সেই বৃত্তান্ত থেকে জন্য যায়, সীতা পরম ক্ষত্রিয় বীর পরশুরামের ঔরসজাত কন্যা।,,,, হরধনু ভঙ্গের পর রামচন্দ্র সীতাকে পত্নীরূপে কাছে পান। পত্নীকে নিয়ে যখন রামচন্দ্র অযোধ্যার পথে অগ্রসরমান তখন তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন মহাবলী পরশুরাম । তাঁর পরমশত্রু রামের পিতা দশরথ। হরধনুর প্রকৃত মালিক স্বয়ং পরশুরাম। তিনি রামকে যা বলেছিলেন, তা পাই পুরাণবিদ ড:দীপক চন্দ্রের গ্রন্থে। তিনি লিখছেন পরশুরামের সংলাপ। “,,, আশ্চর্য তোমার সাহস। তোমার ঔদ্ধত্যের কোনও পরিমাপ হয়না। সীতার বিয়ের জন্য কোনও স্বয়ংবর সভা ডাকা হলো না। রথী মহারথী এল না, শৌর্য বীর্য দর্শনের জন্য কেউ উপস্থিত থাকলো না। সাজানো কতগুলো লোককে সাক্ষী রেখে সীতার পানিগ্রহণ করলে?,
রাম প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেনের ‘রাম কথার প্রাক ইতিহাস’ এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । লেখক লিখেছেনঃ ,,,, রাম নামটি দুদিকথেকে ব্যাখ্যা করা যায় ১) রাত্রির মত,মেঘের মত রং যার,এমন পুরুষ ২) শান্তি, বিশ্বাস,,,,প্রথম অর্থে রাম উদ্ভুত প্রাচীন ইন্দো ইউরোপিয়ান ‘রে’ ধাতু থেকে যার থেকে সংস্কৃতে এসেছে রামী রাত্রি। দ্বিতীয় অর্থে, রাম (রামন) শব্দ এসেছে প্রাচীন ইন্দো ইউরোপিয়ান রেম ( সংস্কৃত রম) ধাতু থেকে। অর্থ আরাম করা। আবার রাম অর্থ বড়ও বোঝায়। আমরা রামদা বলি। অর্থাৎ বড় দা বঁটি। রাম ছাগল। অর্থাৎ বড় আকারের ছাগল। রাম ফল। এক্ষেত্রেও বড় আকারের ফলকে রাম ফল বলা হয়। দশরথের জেষ্ঠ্য পুত্র। তাই কি তাঁর নাম রাম? রামায়ণ মহাকাব্যের মূল চরিত্র রামের আরও প্রামাণ্য অজানা তথ্য দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎবঙ্গ প্রথম খণ্ড গ্রন্থে ১২৫পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদ রামায়ণ। বৌদ্ধ ধর্মই সন্নাসের ধর্ম। এরই প্রতিশোধ হিসেবে গাহস্থ্য ধর্মের রামায়ণ।
আচ্ছা, রামায়ণকে কি মহাকাব্য বলা যায়? তাই নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। এইপ্রসঙ্গেঅ্যাঞ্জেল বুকস অ্যান্ড ভ্যারাইটি স্টোরস কলকাতা থেকে প্রকাশিত মিথ্যাময় ইতিবৃত্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে লেখক শ্রীবিবস্বান আর্য লিখেছেন,,,,, সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমের প্রচারের কল্যাণে যা ইতিমধ্যে জনমানসে শেকড় গেড়ে বসেছে, তা সংক্ষেপে এই এক) রামায়ণ ও মহাভারত দুটি মহাকাব্য। পদবাচ্য। অর্থাৎ মহাকাব্য বলতে যা বোঝায় তাই। দুই) বইদুটি প্রাচীনকালে রচিত। (রচিত শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।) প্রাচীনকালে মানে আজ থেকে হাজার আড়াই বছরেরও আগে, এটাই ধরে নিতে হবে। তিন) দুটোই প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পুরোপুরি না হলেও অংশত আকর গ্রন্থ। চার) বইদুটি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। পাঁচ) বইদুটি প্রথমে সংস্কৃত পরে তামিল তারপর অন্য অনেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। ছয়)বই দুটি রচিত হয়েছিল, লিখিত হয়নি। তখনও লিপি আবিষ্কার হয়নিতাই মুখস্ত করে দুটি কাব্য বাঁচিয়ে রাখা হয়। আবার পুরাণে বলা হয়েছে, বেদব্যাস রচনা করেছেন লিখেছেন শ্রী গণেশ।কোন ভাষায় গণেশ লেখেন তাহলে? সংস্কৃতে? তখন কি সংস্কৃত ভাষা আবিষ্কার হয়েছিল? লেখক বলেছেন, রামায়ণ বা মহাভারতকে মহাকাব্য বলা যায় না। মহাকাব্য কথাটার একটা ইতিহাস আছে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এইচ এইচ উইলসন তাঁর স্যানস্ক্রিট ইংলিশ অভিধানে মহাকাব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈবধচরিত। এই ছটি মহাকাব্য। বিদ্যাসাগর আরওতিনটি মহাকাব্যের কথা বলেছেন। ভট্টিকাব্য রাখবপাণ্ডবীয ও গীতগোবিন্দ। রামায়ণ নামকরণ নিয়েও রহস্য আছে। উইলসন সাহেবের অভিধানে অয়ন শব্দের অর্থ বলেছেন, বাসস্থান। ‘দ্য মেকার্স অফ সিভিলাইজেশন ইন রেস অ্যান্ড হিস্ট্রি’ গ্রন্থের লেখক এল এ ওয়াডেল সাহেব অয়ন শব্দের অর্থ করেছেন দুঃসাহসিক অভিযান বা অ্যাডভেঞ্চার। অর্থাৎ রামের অ্যাডভেঞ্চার। কেউ কেউ রামায়ণের অর্থ করেছেন রামের কীর্তি।আপাতত ভক্তরা রাম নবমী কিভাবে পালন করেন সেটাই আমরা দেখবো। শুদ্র হত্যার বিষয়টি ভুলে শুদ্র ভক্তরাও কিভাবে ভক্তি সহযোগে রামচন্দ্রের জন্মদিন পালন করেন সেটাও দেখবো রামনবমীর শুভদিনে।







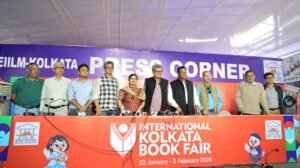














Be First to Comment