জন্মদিনে স্মরণঃ শ মী ন্দ্র না থ ঠা কু র
বাবলু ভট্টাচার্য : ১৮৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম এবং শেষ সন্তান শমীন্দ্রনাথ। ছেলেটি রূপে-গুণে অনেকটাই তার বাবার মতো ছিলেন। ভাল কবিতা পড়তেন, অভিনয় করতেন, ভাল পাঠক ছিলেন। আর তার সবকিছুতেই ছিল যেন একটা বিরল প্রতিভার ছোঁয়া।
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শুরু থেকেই শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেখানকার ছাত্র।
শমী ভীষণ প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের, হয়ত কোথাও তার মধ্যে নিজেরই ছায়া তিনি দেখতে পেতেন। ১৯০২ সালে স্ত্রী মৃণালিনী আর তার কয়েকমাস পরেই কন্যা রেণুকার মৃত্যুর পর মা আর দিদিহারা এই ছোট পুত্রকে রবীন্দ্রনাথ যেন আরো বেশি করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।
সাধারণত রবীন্দ্রনাথ কখনো তাঁর নিজের সন্তানদের সঙ্গে এক শয্যায় শুতেন না। তিনি একলা শুতে ভালবাসতেন, সন্তানরা আলাদা শুত। শমীর কিন্তু খুব ইচ্ছে করত বাবার সঙ্গে শোবার। সে কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ঠিক পাশের লাগোয়া খাটে তার শোয়ার ব্যবস্থা করলেন।
রাতে ঘুমের ঘোরে মাতৃহারা বালক তার হাত বাড়িয়ে দিলে সচেতন রবীন্দ্রনাথও বাড়িয়ে দিতেন তার হাত। বাবার স্নেহ মাখানো হাতকেই মায়ের হাত মনে করে শমী আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। এমন নিবিড় ছিল সেই পিতা পুত্রের সম্পর্ক।
পিতার সেই স্নেহচ্ছায়ায় সেও নিজেকে যেন নিজের অজান্তেই গড়ে তুলছিল তার বাবার যোগ্য করে। আর তারই একটা নিদর্শন যেন ছড়িয়ে আছে আজকের বসন্তোৎসবে। যে বসন্তোৎসব আজ এত প্রিয় অনুষ্ঠান– তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল এই শমীর হাতেই– মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই।
১৯০৭ সালে বসন্তকালে শ্রী পঞ্চমীর দিনে, শমী অন্য অনেককে নিয়ে শান্তিনিকেতনে করে ঋতু উৎসব, যেটিই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বসন্তোৎসবে পরিণত হয়। সেই ঋতু উৎসবে শমী নিজে সেজেছিলেন বসন্ত। অন্যরা কেউ সেজেছিল বর্ষা, কেউ শরৎ।
আর এটি যখন সে করে, তখন সে বছর সে সময় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছিলেন না শান্তিনিকেতনে। ভাবতে অবাক লাগে, একটি দশ বছরের বালক, তার বাবার অনুপস্থিতিতে, তার বাবারই সৃষ্টি অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগ আর উৎসাহে অমন সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন শান্তিনিকেতনের মতো জায়গায়।
বাবার গান তার খুব প্রিয় ছিল। আর তার মধ্যেও বিশেষ করে প্রিয় ছিল– “এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ“ গানটি। যখন তখন, মাঠে ঘাটে এই গানটি শোনা যেত তার খালি গলায়। বেশ কঠিন গান, কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে এই গানটিকেই বেছে নিয়েছিল– সব সময় ঠিক সুরটি লাগাতে না পারলেও। তবে এইটি ছাড়াও আরও কিছু গান তার প্রিয় ছিল।
একটি গানের খাতা ছিল তার, ওপরে লেখা “বন্দেমাতরম”, আর ভেতরে খাতা ভর্তি বাবার গান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রায় এগারোটি গান ছিল সেই খাতায়। মজার কথা সেই সব গানের শেষে বাবার অনুকরণে নিজের স্বাক্ষর– “শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর“, যেন গানগুলি সব তার নিজেরই লেখা!

১৯০৭ সালে দুর্গা পুজোর ছুটি পড়ে গেছে আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসতে হচ্ছে ছোট মেয়ে মীরার অসুস্থতার জন্য। চিন্তা হল শমীর জন্যে, তাকে রাখবেন কোথায়? কলকাতায় সে আসতে চায় না, আবার ছুটিতে শান্তিনিকেতনও তার কাছে একলা ঠেকছে। এই পরিস্থিতিতে স্থির হল শমীকে পাঠানো হবে মুঙ্গেরে– তার বন্ধু সরোজচন্দ্র মজুমদার বা ভোলার সঙ্গে। ভোলারই মামার বাড়ি– মুঙ্গেরে।
রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে চলে এলেন শমীকে যাত্রা করানোর জন্যে। ১৬ অক্টোবর, বিজয়া দশমীর দিন শমীর মুঙ্গের যাত্রা। কেউ ধারণাই করতে পারলেন না– প্রকৃত অর্থে সেটিই হল শান্তিনিকেতন থেকে শমীর বিসর্জনের যাত্রা, আর কোন দিনই সে ফিরে আসবে না সেখানে।
একমাস পরেই কলকাতায় এল উদ্বেগপূর্ণ খবর– শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে কলেরায় আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে মুঙ্গের রওনা হয়ে গেলেন এখান থেকেই একজন ডাক্তার নিয়ে। শান্তিনিকেতন থেকে গেলেন সেখানকার শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।
মুঙ্গেরে যে বন্ধুর মামার বাড়ীতে শমী ছিল, তার দুই মামাই ছিলেন ওখানকার বিশিষ্ট ডাক্তার। এছাড়া ওখানকার অন্যন্য ডাক্তাররাও ছিলেন। ছিলেন কলকাতা থেকে যাওয়া ডাক্তারও। চিকিৎসা চলছিল এলোপ্যাথিক আর হোমিওপ্যাথিক– দুই ভাবেই। অর্থাৎ চিকিৎসার কোন ত্রুটিই রাখা হয় নি।
কিন্তু যখন কারোর ডাক পড়ে ওপার থেকে, তখন সেই ডাককে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। তাই সারা রাত চলল যুদ্ধ, শেষ রাতে হার মানতেই হল। চলে গেলেন শমী, ১৯০৭ সালের ২৪ নভেম্বর, বাংলা ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ, তার মায়ের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বছর পরে।
রবীন্দ্রনাথ তখন সেই বাড়ীতেই উপস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য, যে রবীন্দ্রনাথ এর আগে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, পিতা– সবার শেষ সময়ে তাঁদের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত থেকেছেন, হাতে ধরে বিদায় দিয়েছেন তাঁদের, সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু তাঁর পরম প্রিয় শমীর শেষ সময়ে তার পাশে রইলেন না। রইলেন পাশের ঘরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। কিছুক্ষণ পরে ভূপেনবাবুকে ডেকে তিনি শান্ত ভাবে বললেন- “এ সময়ে আমার যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম। এখন অবশেষে যাহা কর্তব্য আপনি করুন।“
মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে তার দুয়ারে প্রিয়জনকে এগিয়ে দেওয়ার সময় এ এক নতুন রূপ– শুধু কবি নয়, মানব জীবনের অনেক ঊর্ধে অন্তর্মুখী এক সাধক রবীন্দ্রনাথের।
শমীর শেষকৃত্য হয়ে গেল মুঙ্গের শ্মশানেই, রবীন্দ্রনাথ গেলেন না। ফিরে এসে সবাই দেখল– তিনি তখনো পাথরের মতো স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে বসে। সবাই তাঁর অবস্থা দেখে একটু চিন্তায় পড়লেন। এমন দমবন্ধ করা শোকের সময়– এই ভাবে সমস্ত আবেগকে সংহত করে, এইভাবে স্থির, নিশ্চল, গম্ভীর হয়ে বসে থাকা ভাল লক্ষণ নয়। তবে এইসময় অন্যদের কাঁদতে দেখে তাঁর চোখ থেকেও জল গড়িয়ে পড়ল, সাধক স্তর থেকে কিছুটা স্বাভাবিক লক্ষণে নামলেন রবীন্দ্রনাথ।
একটু চিন্তামুক্ত হলেন অন্যরা- মানব জীবনে শোকের সামান্য হলেও কিছু বাহ্যিক প্রকাশ তো দরকার। সেই রাত্রেই শান্তিনিকেতন ফেরার ব্যবস্থা হল। ফেরার সময় ভূপেনবাবুর মামা সাহেবগঞ্জে ওঁদের জন্য – খাবার নিয়ে এলেন।
রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বললেন তাঁর সঙ্গে। পরে তিনি যখন অন্যদের থেকে মুঙ্গেরের ঘটনা জানতে পারলেন তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কারণ, কবির সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি একটুও বুঝতে দেননি যে কয়েকঘন্টা আগেই তিনি তার সবচাইতে আদরের ছোট্ট ছেলেকে চিরবিদায় জানিয়ে ফিরছেন।
শান্তিনিকেতনে ফিরেও সেই এক অবস্থা। কারোকেও জানানো হয়নি শমীন্দ্রনাথের বিদায় সংবাদ– তাই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সে সংবাদ যখন সবাই শুনলেন রবীন্দ্রনাথরা মুঙ্গের থেকে ফিরে আসার পর, তখনও রবীন্দ্রনাথ শান্ত নিশ্চুপ। কারোর মুখে কথা নেই, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু “রবি, রবি“ বলতে পারছেন, আর কিছু কথা তাঁর মুখে আসছে না।
রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অচঞ্চল। শোক তাঁকে আঘাত করছে কিন্তু পরাভূত করতে পারছে না- “আরো আঘাত সইবে আমার সইবে আমারো/আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝঙ্কারো”– এটাই যেন তাঁর মনোভাব।
এই সহ্য শক্তি নিয়ে তিনি পরে অবলা বসুকে লিখলেন– “ঈশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা শিরোধার্য করিয়া লইব। আমি পরাভূত হইব না”। জগদীশ বসুকে লিখছেন– “আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ, এত অভাব, এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষ রূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়”।
মনের এই অপরিসীম শক্তি থেকেই তিনি শমীর জামাকাপড় ভুবনডাঙ্গার ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাইলেন। শমীন্দ্রনাথ একটি সাদা খাতায় ডায়রি লিখতেন, তাতে কতকগুলি সাদা পাতায় তিনি আগে থেকে তারিখ দিয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর সেই খাতা ওলটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন– ঠিক যেদিন শমী মারা গেছে, সেইদিন পর্যন্ত ডায়রিতে তারিখ দেওয়া আছে, তারপর আর নেই। অবাক কবি বললেন– “এর থেকে মনে হয় এমন একজন আছেন, যাঁর কাছে আমাদের ভবিষ্যতও অজানা নয়”।
শমীর মৃত্যুতেও রবীন্দ্রনাথের কোন কাজে ছেদ পড়েনি। গান রচনা চলেছে। মাঘোৎসবের প্রস্তুতি চলেছে। ‘গোরা’ উপন্যাসের কিস্তি ঠিক সময়ে জমা পড়েছে। শিলাইদহের কাজ চলেছে– সব কিছু চলেছে যেমন চলার।
আমার প্রাণের ‘পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে–
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।
সে চলে গেল, বলে গেল না– সে কোথায় গেল ফিরে এল না।

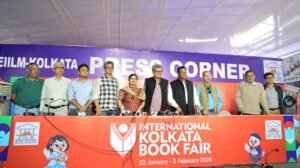


















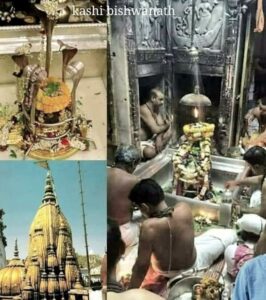
Be First to Comment