শু ভ জ ন্ম দি ন জঁ লু ক্ গ দা র
বাবলু ভট্টাচার্য : তার গদ্য খুবই জটিল এবং দুরূহ, কখনো কখনো তার ছবির চেয়েও দুর্বোধ্য। কিন্তু তাঁর লেখা ও তাঁর সিনেমা প্রায় একই শিল্প, কারণ আত্মপ্রকাশের সব কটি মাধ্যমের মধ্যেই একটা স্পষ্ট ধারাবাহিকতা রয়েছে।
গদারের ছবির স্টাইল তার একান্তই নিজস্ব। তার আগে চলচ্চিত্রে এ ধরণের স্টাইলের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। এতদিনকার বর্ণনা ভঙ্গিটাকে গদারই ভেঙে দিয়েছেন। পাশাপাশি এতখানি সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা খুব কম পরিচালকের ছবিতেই দেখা গেছে।
গদার কিন্তু বিষয়কে অগ্রাহ্য করেননি, বিষয় আর রীতির মধ্যে এতখানি ভারসাম্য আর কেউ রক্ষা করতে পারেননি, কখনো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নেয়া যায়— প্রায় এরকম। রূপ ও বিষয়ের এতখানি সুষমতা আগে দেখা যায়নি। চলচ্চিত্রের-নন্দনতত্বের এতখানি আত্মবিরোধী বৈশিষ্ট্য আমরা অন্য পরিচালকের ছবিতে দেখিনি বলা যায়।
কবিতার প্রতি গদারের কৃতজ্ঞতা আজীবন। প্রেমিক পুরুষ ও রমণীয় অন্তর্লীন সম্পর্কের আয়নাতেই যিনি প্রতিফলিত করতে চান আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সংকটের আলো- ছায়াময় দৃশ্যমালা, সোনালী ডানার চিলের মতো কেবলই হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসেন যিনি। আমাদের ভুল হবে যদি ভাবি তার পর্যটনের সমস্ত পথটাই প্রেতচক্ষু অন্ধকার দিয়ে মোড়া অথবা মৃত সব উল্কাপিন্ডের অট্টহাসি দিয়ে কাঁপানো।
একটু মনস্ক হলেই আমাদের চোখে পড়বে তার অনাবেগের ভূবনেও চাঁদ ওঠে, নক্ষত্রসভায় নাচে জ্যোৎস্না, বাঁশি বাজায় মেঘ, পরস্পরকে চুম্বনে এবং আলিঙ্গনে জড়ায় আকাশ এবং সমুদ্র। সেই কারণেই তার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ‘ফ্রিকোয়েন্টলি রিপালসিভ’ এবং ‘ডেলিবারেটলি সেলফ কনট্রাডিকটারী’র আগে বসাতে হয় ‘কমপেলিংলি টেন্ডার’।
বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটা সত্যি যে গদার ভালোবাসাকে বড় বেশী ভালোবাসেন। আর ভালোবাসাকে ভালোবাসার সূত্রেই ছবি, কবিতা এবং গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। তাঁর যে-কোনো একটি উৎকৃষ্ঠ ছবির দিকে মনোযোগ ছড়ালেই চোখে পড়বে একটা গোপন ঝরণা, যেখানে অবিরল উদগীর্ণ হয়ে চলেছে রূপোলীজলরেখা। এই বিচ্ছুরণের নামই ভালোবাসা।
বিগত তিন দশক ধরে চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমটিকে একটি বৈপ্লবিক রূপগ্রহণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে গদারের কাজকর্মের বৈশিষ্টগুলি। ‘নিউ ওয়েভ’ ঘরানার ছবি নির্মাণে রাজনীতি ও শিল্পকলার প্রতি র্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতে হাতে চালানো ক্যামেরা, জাম্পকাট, ফ্লাশকাট ইত্যাদির দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, ছবির মধ্যে দর্শনমূলক ডায়ালেকটিক্স পরিস্ফুটিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবহারে, সিনেম্যাটিক ধারাবাহিকতার প্রতি বিরাগে- সব মিলিয়ে গদার আজ কিংবদন্তির নায়ক।
স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গদার Latin Quarter’s Cine Club এবং সিনেমাথেক-এ নিয়মিত যাতায়াত করছেন। ওখানেই তিনি পরিচিত হন আঁদ্রে বাজাঁ, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, এরিক রোমার, জাক্ রিভেতের সঙ্গে।
১৯৫০ সালে যখন তার বয়স ২০ বছর রোমার এবং রিভেতের সঙ্গে তিনি Gazette du cinema বার করেছেন, বেশ কয়েকটি সংখ্যা। তখন রোমার এবং রিভেত তাদের প্রথম শর্ট ফিল্মগুলো তুলেছিলেন, বেশ কটিতে গদার অভিনয়ও করেন।
’৫২ থেকে ’৫৪-র মধ্যে লিখেছেন ‘কাই দ্যু সিনেমা’য়, ব্যবহার করেছেন ‘হানস লুকাস’ এই ছদ্মনাম। এই সময় বাবার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছেন।
অল্প সময়ের জন্যে প্যারিসে ফিরে এসে তিনি সুইজারল্যান্ডে ফিরে যান এবং সেখানে Grand dixenence dam-এ শ্রমিকের কাজ নেন। সেই কাজে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাই দিয়ে তাঁর প্রথম ডকুমেন্টারি ‘Oparation Beton ঐ Dam তৈরির বিষয় নিয়ে। তোলেন ১৯৫৪ সালে। নিজেই সম্পাদনা করেন। ’৫৫ তে জেনেভায় দ্বিতীয় ছোট ছবি ১০ মিনিটের Une Femmemme coquette’ চিত্রনাট্য, পরিচালনা, ফটোগ্রাফী এবং সম্পাদনা- সবই নিজে করেন। গল্প নেন মোপাঁসা থেকে। তারপর প্যারিসে ফিরে আসেন।
১৯৬৮ সালে সেই লেখাগুলো নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় ‘Jean Luc Godard par Jeaean Luc Gododard.’ এই বই পড়লেই বোঝা যাবে তত্ত্বকে কিভাবে কার্যে রূপায়িত করা যায় তার আদর্শ নমুনা রয়েছে গদারের ছবিতে।
১৯৬১ সালে গদার বিয়ে করেন অভিনেত্রী আনা কারিনাকে। ১৯৬৪ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তাঁদের। গদারের কয়েকটি ছবিতে আনা অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন।
জঁ লুক্ গদার ১৯৩০ সালের আজকের দিনে (৩ ডিসেম্বর) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন।




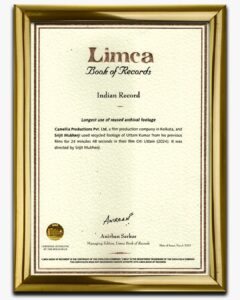






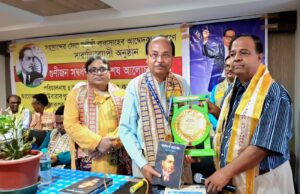



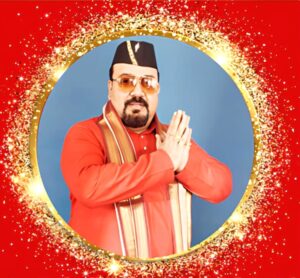


Be First to Comment